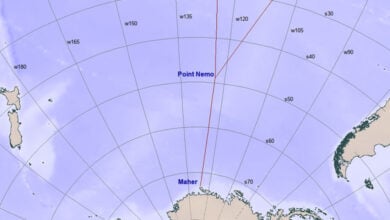ভরদুপুরে প্রেতাত্মাকে অবিকল মানুষের বেশে দেখা
কয়েক বছর আগে এই পুকুরে স্নান করতে গিয়ে একজন মারা যায় জলে ডুবে। তারপর থেকে এই প্রেতাত্মাকে অবিকল মানুষের বেশে অনেকেই দেখেছে।

১৯৫৬ সাল। তখন আমার বয়স পাঁচ। সেই সময় আমাদের দিন চলে না মাস বত্রিশ অবস্থা। অভাবের সংসার। বড়দিদির তখন সচ্ছল অবস্থা। চার ছেলে। মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন মধ্যমগ্রামে দিদির বাড়িতে। উদ্দেশ্য পড়াশোনা করে মানুষ না হই, অন্তত অমানুষ যেন না হই। একদিন, ওই পাঁচ বছর বয়সে কাঁদতে কাঁদতে বড় জামাইবাবু’র হাত ধরে উঠে বসলাম কয়লার ইঞ্জিনের রেলগাড়িতে। তখন মধ্যমগ্রাম স্টেশনে কোনও প্ল্যাটফর্ম ছিল না। সোদপুর রোড ধরে চৌমাথার দিকে এগলে পথের দু’পাশের বড় বড় তেঁতুল আর আমগাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবে বাঁ-পাশে কালিবাড়িটা তখন ছিল, আজও আছে তবে জাঁকিয়ে নয়।
সেই সময় ছোট জমিদার ব্যানার্জিবাবুর নামানুসারে অল্প কয়েক ঘর-বসতি নিয়ে হয় ব্যানার্জিপাড়া। ওখানেই দিদির বাড়ি। অনেক পরে ব্যানার্জিপাড়া একাকার হয়ে যায় বঙ্কিমপল্লিতে।
দিদির বাড়ির সামনে তখন ছিল বিশাল খেলার মাঠ, আজও আছে। মাঠের দক্ষিণ দিকে মণি বোসের বাগানবাড়ি। চলতি কথায় বোসবাগান। আমি তাঁকে কোনওদিন দেখিনি তবে তিনি যে অত্যন্ত রুচিবান ও শৌখিন ছিলেন তা বাগান দেখলে তখন বুঝিনি তবে এখন বুঝি। ওই বাগানে কী ছিল না? একটা বড় পুকুর পাড়ে বিশাল দুটো। ‘হাড়ির তাল’ গাছ, পাড়ে সবেদা গাছ, বাগানে গোতাল গাছ, চালতা গাছ, জলপাই ও কমলালেবু, কামরাঙা, তেজপাতা, করমচা, পোস্ত, কী ছিল না এই বাগানে! গোল বারান্দার একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির সামনে সোনালি রঙের ছোট্ট একটা ঘটি বাঁশ গাছের ঝাড় ছিল। বাঁশের একটা গাঁট থেকে আর একটা গাঁট পর্যন্ত একেবারে আগেকার দিনের পেটমোটা ঘটির মতো। বাড়ির সামনে বড় রজনীগন্ধার একটা আর একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ।
মাঠের পশ্চিমে গুহ সাহেবের বাগান। আসলে বিজয় গুহ’র আমবাগান বাড়ি। অসংখ্য আমগাছ ভরা। গুহ থেকে বিজয়বাবু হলেন গুহসাহেব। এখন ঘনবাগান সাফ হয়ে দাঁড়িয়ে হয়েছে ‘বিজয়নগর’।
মাঠের পূর্বদিকে তাকালে বুড়িমার বাগান। আমরা বলতাম বুড়ির বাগান। খানা-কেটে জমির সীমানা চিহ্নিত করা। খানার পাশ দিয়ে পালপাড়ার দিকে এগলে বিশাল বিশাল আমগাছ। বলা যায় আম্বাগান। বেশ গভীর, বেশ ঘন জঙ্গল। বোসবাগান লাগোয়া দুটো ডোবা ছিল। প্রতিবছর বর্ষার গ্রামের পুকুর ভরে গেলে খানা-খন্দ দিয়ে মাছ ঢুকত ডোবায়। নিজেও জল কমলে মাছ ধরেছি। ডোবা আর আমবাগান বাদ দিলে বাকি বিস্তীর্ণ জমি ধানক্ষেত। তার পাশ দিয়ে লম্বা ফালি জায়গায় আবার আমগাছের সারি, তাও বেশ গভীর। এর পাশে প্রতিবছর আলু, মুলো, শসা, ভেন্ডি ইত্যাদির চাষ হত।
বুড়িমার বাড়িটা ছোট। একতলা দালান বাড়ি। এই বাড়ির পিছন দিকটায় যে পুকুরটা ছিল সেটা বেশ বড়। পুকুরের পাশে আশফল আর ফলসা গাছ। আর পূর্বদিকে পুকুরের কোণে দুটো আমগাছ। এরপর সম্পূর্ণ বিশাল জায়গা জুড়ে হিমসাগর আর অসংখ্য পেয়ারা গাছ। এককথায় পিয়ারা বাগান বলাই ভালো। বুড়িমার বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল বিশাল একটা কালোজাম গাছ। জামগুলো এত বড় হত, আর গাছটা এত বড়, এমনটা আমার নজরে পড়েনি কখনও।
বুড়িমার বাগানে মালির কাজও দেখাশোনা করত একটা সাঁওতাল পরিবার। এদের দেখেছি বিষধর সাপকে রান্না করে খেতে। ধানখেতে ধানের মরশুমে বেশ বড় বড় ইঁদুর মাটিতে গর্ত করে ধান নিয়ে ওখানে রাখত। ওই গর্ত থেকে ইঁদুর ধরে রান্না করে খেত। বুড়িমার বাগানে চোখে দেখেছি নানান ধরনের বিষধর সাপ, শজারু, বোনমুরগি, হায়না, গোসাপ, বুনো খরগোশ যাকে বলে খটাস (খয়েরি রঙের এর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু), বনবিড়াল। আর এমন কোনও পাখি নেই যা বুড়ির বাগানে ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিয়ালের কীর্তন যেন দস্তুর।
বুড়িমার বাগানের পাশেই বিশাল এলাকা জুড়ে গঙ্গাধরের বাগান। গঙ্গাধর মালিকের না মালির নাম তার আমার জানা নেই। ওই নামেই বাগান সুখ্যাত। গোটা বাগানটাই ছিল সুমিষ্ট আমগাছে ভরা। আর ছিল অসংখ্য সবেদা গাছ। ইয়া বড় বড় সবেদা হত। গাছেই পাকত। পাখিতে খেত। আমিও খেতাম। প্রচুর লিচুগাছ ছিল। এত সুস্বাদু লিচু বাজার থেকে কেনা কোনও লিচুতে এমন স্বাদ আমি পাইনি কখনও।
মোটের ওপর আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে আমার দেখা মধ্যমগ্রামে জঙ্গলে ঘেরা বঙ্কিম পল্লির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন নির্মল আনন্দময় ও সৌন্দর্যেভরা প্রাকৃতিক রূপ ও রসকথা, তবে রাতে বিদ্যুতের আলো ছিল না। সন্ধ্যার পর গোটা মধ্যমগ্রাম যেন প্রেতপুরী।
আমার বড়দিদির বাড়ির উত্তর কোণে ধীরাজ নাগ, তার উলটোদিকে প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। ঠিক এর বিপরীতের বাড়িটাই রবিদার বাড়ি। রবি ঘোষ। কী কাজ করতেন তিনি তা ত আমার স্মৃতিতে নেই। তবে রবিদার একমাত্র নেশা ছিল মাছধরা পাড়াসুদ্ধ লোক রবিদাকে ‘মাছুড়ে’ বলত। শুকনো ডাঙায় ছিপ ফেলে বসে থাকলে কোনও না কোনওভাবে তাঁর ছিপে মাছ উঠবে উঠবে। এটাই যেন দস্তুর।
ছোটবেলায় আমার চুরি করার অভ্যাস ছিল। কারও বাগানে বাড়িতে ফলের গাছ থাকলে, সেই গাছে ফল পেকে থাকলে আমার নজরে পড়লে সে ফলটা চুরি করতামই। প্রতিবেশীদের বাড়ির ফুল চুরি করতাম ভোরে, আবছা অন্ধকার থাকতে। চুরি করার মোক্ষম সময়টা ছিল যে কোনও ছুটির দিনে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। নেশা ছিল না। তবে ছিপে কেঁচো গেঁথে মাছ ধরতে খুব ভালো লাগত।
তখন আমার বয়স বছর দশ-এগারো হবে। স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে। দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কাঠফাটা রোদ্দুর ভাবলাম, যাই, বুড়ির বাগানে, পুকুর থেকে মাছ ধরে আনি। এ মালি ঘর থেকে বেরবে না। নিশ্চিন্তে মাছ ধরা যাবে। ভাবামাত্র বেরিয়ে পড়লাম ছিপ আর কোঁচা নিয়ে। বাড়ি থেকে হাঁটাপথে আমবাগানবেষ্টিত বুড়ির বাগানের পুকুর মিনিট চার-পাঁচেক।
দুরন্ত রোদ্দুরের হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম পুকুর পাড়ে আমগাছের ছায়ায়। পুকুরে চোখ পড়তেই দেখি চেনা চেহারা – রবিদা। ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। রোদের জন্য মাথায় একটা গাম ছড়ানো। মুখটা ভালো করে দেখা না গেলেও চেহারাটা চেনা, পরিচিত। দূর থেকে দেখলাম একটা বিঘত খানেক লম্বা মাছ বড়ঁশি থেকে খুলে খ্যাড়ইতে (বাঁশের তৈরি মাছ রাখার পাত্র) রাখল। এবার দেখছি খালি ছিপ ফেলছে আর ফটাফট মাছ তুলছে।
ধৈর্য ধরতে পারলাম না। গরমকাল। পুকুরে জল অনেকটাই খানিকটা নেমে গিয়ে বসে পড়লাম রবিদার থেকে হাত ২০/২২ দূরে। বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে ছিপ ফেললাম। মিনিট ৫/৭ গেল ফাতনা নড়ে না। রবিদার ফাতনা অনবরত নড়ছে আর মাছ উঠছে একটু হতাশ হয়েই বললাম, রবিদা, কী ব্যাপার বলুন তো, একটা মাছও তো দেখছি খাচ্ছে না।
কথাটা বলে আড়চোখে দেখলাম, হাতের ইশারায় বললেন বসে থাক, পাবি। মুখে কোনও কথা বললেন না। তবে রবিদার ধরাতে ছেদ পড়ছে না।
এইভাবে আরও পাঁচ-দশ করে কেটে গেল প্রায় আরও মিনিট কুড়ি। একটা মাছও আমার বঁড়শিটা স্পর্শ করল না। হতাশ হয়ে ছিপটা হাতে নিয়ে ‘আমার কপালে মাছের ভাগ্য নেই’ বলতে বলতে রবিদার দিকে কয়েক পা এগতেই দেখি রবিদা নেমে গেলেন হাঁটু জলে।
আমি বললাম, ও রবিদা, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন জলে নেমে’। মুখে কোনও কথা নেই। গামছাটা এক ঝলক মুখ থেকে সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম, কে যেন ঘাড়ে একটা কঙ্কালের মাথা বসিয়ে দিয়েছে। এবার সারা দেহটা জলে মিলিয়ে গেল সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে রোদের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল যেন নিমেষে। সর্বাঙ্গ আমার ভারী হয়ে গেল। দরদর করে ঘামতে লাগলাম। ওই মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। শিউরে উঠতে লাগল দেহমন। চিৎকার করে যে কাউকে ডাকার ক্ষমতা আমার চলে গিয়েছে। বাক্রোধ হয়ে গিয়েছে। এই মুহুর্তে কিছু ভাবতে পারছি না। বাড়িতে ফিরব, পা চলছে না। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। অস্তিত্বটা লোপ পেয়ে গিয়েছে ভয়ে। হাতে ধরা ছিপ কখন হাত থেকে পড়ে গিয়েছে টের পাইনি। নিশ্চল দাঁড়িয়ে পুকুরের এক পাশে।
কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানা নেই। সাঁওতাল মালি এসে গায়ে ধাক্কা দিতে হুঁশ এল। তখনও রোদ আছে। মনে হল তাপটা যেন একটু কমেছে।

ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা আনুপূর্বিক জানালাম মালিকে। আমার কথা শুনে মালি এতটুকুও বিস্মিত হল না। উলটে জানাল আমি যেন আর কোনওদিন দুপুরে পুকুরে না আসি। প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে ২টোর মধ্যে এখানে এলে ওর দেখা অনেকেই পেয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে এই পুকুরে স্নান করতে গিয়ে একজন মারা যায় জলে ডুবে। তারপর থেকে এই প্রেতাত্মাকে অবিকল মানুষের বেশে অনেকেই দেখেছে।
বাড়িতে কোনওরকমে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলাম এক গা জ্বর নিয়ে। সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা বাড়ির পর ডাক্তার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ি। ওষুধ লিখেছিলেন। খেলাম। জ্বর কমল না। দিন দুই পর ‘কল্যাণ সমিতি’র দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেখিয়ে ওষুধ খেলাম। কিছুতেই জ্বর ছাড়ল না। অগত্যা বড় জামাইবাবুর সঙ্গে এলাম কলকাতায়।
বাড়িতে এসে সমস্ত ঘটনার কথা জানালাম মাকে। সব কথা শুনে সেদিন মা বলেছিল, ‘কোনও ডাক্তারের বাপের ক্ষমতা নেই তোর জ্বর সারাতে পারে। হাওয়া বাতাস লেগেছে।’
এরপর মা আমাকে পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় নিয়ে গেল স্থানীয় একটা মাজারে। নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসার সময় ধর্মার্থীরা মাথায় ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে দিলেন। দিন কয়েকের মধ্যে জ্বর পালাল গা ছেড়ে। সুন্দর সুস্থ হয়ে উঠলাম আমার অক্ষরজ্ঞানহীন গর্ভধারিণী মায়ের একান্ত ও গভীর বিশ্বাসে।